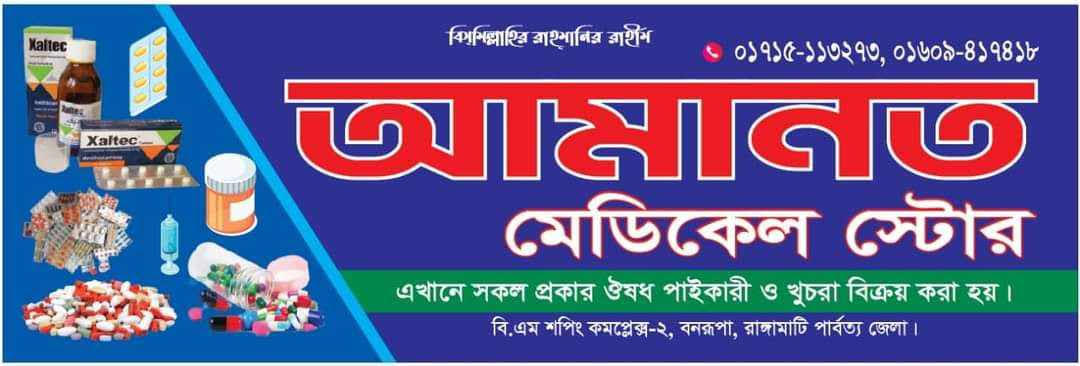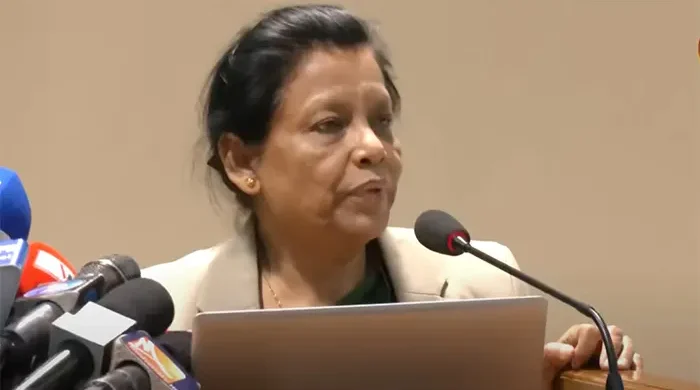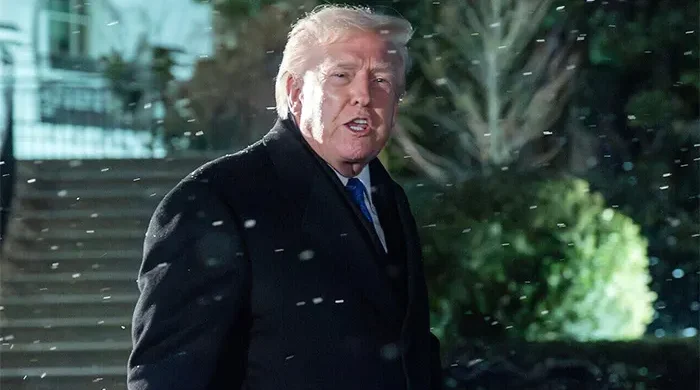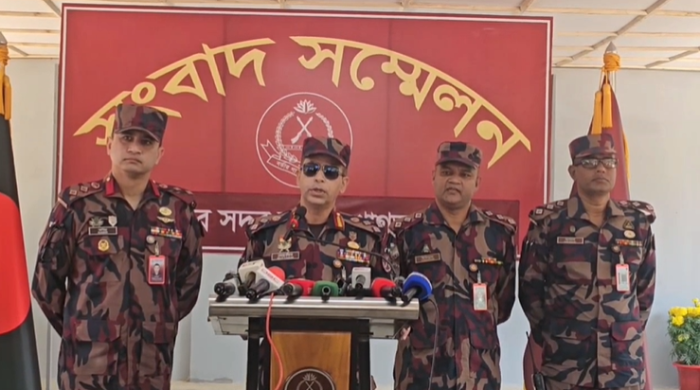মোবাইল কোর্টে কারাদণ্ড দেওয়া যাবে না–কমিশনের সুপারিশ

- আপডেট সময় বুধবার, ৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫
- ১৫৯ দেখা হয়েছে

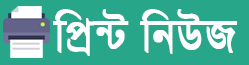
ডেস্ক রির্পোট:- মোবাইল কোর্ট (ভ্রাম্যমাণ আদালত) আইন-২০০৯ অনুযায়ী নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটরা তাৎক্ষণিক কোনো অপরাধ আমলে নিয়ে বিচার করতে পারেন। ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে অপরাধ সংঘটিত হলে ঘটনাস্থলেই অপরাধ আমলে গ্রহণ করতে পারেন তারা। বর্তমানে পরিবেশ ও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, শ্রম আইন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনসহ ১১৬টি আইনের অধীনে সংঘটিত অপরাধ আমলে নেওয়ার এখতিয়ার রয়েছে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের। অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযোগ স্বীকার করলে তাকে সর্বোচ্চ দুই বছরের কারাদণ্ড এবং আইনে নির্ধারিত সীমার মধ্যে যে কোনো পরিমাণ অর্থদণ্ড আরোপ করতে পারেন। কিন্তু বিচারের মৌলিক বৈশিষ্ট্য অনুসরণ না করেই নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের দুই বছরের কারাদণ্ড আরোপ করার বিধান রহিত করার সুপারিশ করেছে বিচার বিভাগীয় সংস্কার কমিশন।
সংস্কার কমিশন তার প্রতিবেদনে বলেছে, মোবাইল কোর্ট আইনের মাধ্যমে একজন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে (নির্বাহী হাকিম) বিচারিক ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে, যা নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথকীকরণের নীতির পরিপন্থি। এই আইন অনুযায়ী একজন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বিচারের মৌলিক বৈশিষ্ট্য অনুসরণ না করেই অভিযুক্তের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে ২ (দুই) বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড আরোপ করতে পারেন, যা সংবিধানের ৩২, ৩০ ও ৩৫ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত মৌলিক অধিকারের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। পক্ষান্তরে এর চেয়ে কম দণ্ড আরোপের ক্ষেত্রেও একজন জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকে ফৌজদারি কার্যবিধি অনুসারে বিচারের কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটদের (বিচার বিভাগীয় হাকিমদের) পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ আদালতের পরিধি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করা এবং যেসব পরিস্থিতিতে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটদের মাধ্যমে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা যথাযথ ও বাস্তবসম্মত হবে না, শুধু সেই সব ক্ষেত্রে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা বাঞ্ছনীয় বলে সংস্কার কমিশন তার প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে।
বিচার বিভাগের প্রয়োজনীয় সংস্কারের প্রস্তাব করতে গত ৩ অক্টোবর আপিল বিভাগের সাবেক বিচারপতি শাহ আবু নাঈম মমিনুর রহমানের নেতৃত্বে আট সদস্যের সংস্কার কমিশন গঠন করে সরকার। এরপর থেকেই কমিশন সরেজমিন বিভিন্ন আদালত পরিদর্শন, মতবিনিময়সহ নানা কার্যক্রম গ্রহণ করে। দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনার পর বিচার বিভাগের মোট ৩০টি বিষয়ে সংস্কারের প্রস্তাব করে প্রতিবেদন চূড়ান্ত করেছে কমিশন।
এসব বিষয়ের মধ্যে রয়েছে সুপ্রিম কোর্টে বিচারক নিয়োগ ও শৃঙ্খলা, অধস্তন আদালতে বিচারক নিয়োগ ও চাকরির শর্তাবলি, সুপ্রিম কোর্টে আলাদা সচিবালয় স্থাপন, আদালত ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ, স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠা, স্বতন্ত্র ফৌজদারি তদন্ত সংস্থা গঠন, বিচারপ্রার্থীদের হয়রানি লাঘব, দুর্নীতি বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ, আইনগত সহায়তা কার্যক্রম ও বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা কার্যকর করা, প্রচলিত আইনের, আইন পেশার ও আইন শিক্ষার সংস্কার, মিথ্যা ও হয়রানিমূলক মামলা প্রতিরোধ, মামলার জট হ্রাস, মোবাইল কোর্ট, গ্রাম আদালতসহ মোট ৩০টি বিষয়ে সংস্কারের প্রস্তাব করা হয়েছে।
জানতে চাইলে বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের সদস্য ব্যারিস্টার তানিম হোসেন শাওন বলেন, ‘সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে। বুধবার প্রতিবেদনটি উপদেষ্টা পরিষদের কাছে জমা দেওয়া হবে। কমিশন ৩০টি বিষয়ে আলোকপাত করেছে। একটি সারসংক্ষেপও জমা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রতিবেদন জমা দেওয়ার পর ঐক্য কমিশন এই সুপারিশগুলো নিয়ে কাজ করবে। বিচার বিভাগীয় সংস্কার কমিশনের পক্ষ থেকে বিচারপতি এমদাদুল হক ঐক্য কমিশনের সঙ্গে কাজ করবে। সুপারিশের মধ্যে কোনগুলো স্বল্পমেয়াদি ও কোনগুলো দীর্ঘমেয়াদি বাস্তবায়নযোগ্য, তা বিশ্লেষণ করবে। এরপর রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে এসব নিয়ে বৈঠক হবে।’
‘সব বিভাগে হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ’:
রাজধানীর বাইরে প্রশাসনিক বিভাগীয় সদরে হাইকোর্ট বিভাগের স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপনের পাশাপাশি উপজেলা পর্যায়ে দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতের কার্যক্রম সম্প্রসারণের প্রস্তাব করেছে সংস্কার কমিশন। একই সঙ্গে সুনির্দিষ্ট কিছু জেলা আদালতে প্রয়োজন অনুসারে এক বা একাধিক বাণিজ্যিক আদালত স্থাপন করা যেতে পারে। আদালত ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ বিষয়ে সংস্কার কমিশন এমন সুপারিশ করেছে।
এতে বলা হয়েছে, প্রতিটি স্থায়ী বেঞ্চ কোন কোন এলাকা থেকে উদ্ভূত মামলা গ্রহণ করতে পারবে, তা সুনির্দিষ্ট করে দিতে হবে। বিচারকাজ পরিচালনা এবং রায়, আদেশ, নির্দেশ ইত্যাদি প্রদানের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগের এখতিয়ারের পূর্ণাঙ্গতা বজায় রাখতে হবে। অর্থাৎ স্থায়ী বেঞ্চগুলো স্থাপনের কারণে দেশব্যাপী কর্তৃত্ব প্রয়োগের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগের এখতিয়ার কোনো ভৌগোলিক সীমারেখা দিয়ে বিভাজিত হবে না এবং রাষ্ট্রের একক চরিত্র ক্ষুণ্ন হবে না। এতে বলা হয়, প্রধান বিচারপতি স্বতঃপ্রণোদিতভাবে বা কোনো স্থায়ী বেঞ্চে বিচারাধীন মামলার কোনো পক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কোনো যৌক্তিক কারণে বা ন্যায়বিচারের স্বার্থে ওই মামলা অন্য কোনো যথাযথ বেঞ্চে স্থানান্তর করতে পারবেন। আরও বলা হয়েছে, স্থায়ী বেঞ্চগুলো সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য আদালত ও সহায়ক কার্যালয়, বিচারক ও সহায়ক জনবলের জন্য উপযুক্ত বাসস্থানসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো স্থাপন এবং প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে। সব স্থায়ী বেঞ্চ একই সঙ্গে কার্যকর করা কঠিন বিবেচিত হলে প্রয়োজনে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে বিভাগীয় সদর দপ্তরগুলোতে স্থায়ী বেঞ্চ কার্যকর করা যেতে পারে।
মোবাইল কোর্ট:
মোবাইল কোর্টের যৌক্তিকতা তুলে ধরা হয়েছে সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে। এতে বলা হয়েছে, মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট অপরাধ সংঘটিত হওয়ার স্থানেই দ্রুততার সঙ্গে তার প্রতিকার করতে সক্ষম হন। এভাবে অপরাধীদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক শাস্তির উদাহরণ সৃষ্টি হওয়া একই ধরনের অপরাধের প্রবণতা হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে জটিল ও দীর্ঘ প্রক্রিয়া এড়িয়ে স্বল্পসময়ে বিচারিক কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। ফলে জনগণের কাছে তা আইন প্রয়োগ সম্পর্কে একটা ইতিবাচক ধারণা তৈরিতে সহায়তা করে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মোবাইল কোর্ট আইনের সাংবিধানিকতা বিষয়ে আপিল বিভাগে বিচারাধীন মামলায় বিষয়টির চূড়ান্ত মীমাংসা হবে। এরই মধ্যে বাস্তবতার নিরিখে মোবাইল কোর্টের প্রয়োজনীয়তা এবং এর সমান্তরালে মোবাইল কোর্ট আইনের সাংবিধানিক ও আইনগত অসংগতিগুলোর বিবেচনায়, সংস্কার কমিশন প্রস্তাব করেছে। প্রস্তাবে আইন সংশোধন করে মোবাইল কোর্টের কারাদণ্ড আরোপের ক্ষমতা রহিত করার কথা বলা হয়েছে। মোবাইল কোর্ট স্বীকারোক্তির ওপর ভিত্তি করে আইনে নির্ধারিত অর্থদণ্ড আরোপ করতে পারবে এবং তার তল্লাশি এবং জব্দকৃত বস্তু বিলিবন্দেজ সম্পর্কিত ক্ষমতাও বহাল রাখার কথা বলা হয়েছে।
এতে বলা হয়েছে, অর্থদণ্ড আদায়ে জটিলতা নিরসনে সাধারণ কর্মঘণ্টায় মাধ্যে মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় গুরুত্বারোপ করা বাঞ্ছনীয়। ক্ষেত্রবিশেষে, সাধারণ কর্মঘণ্টার বাইরে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার একান্ত প্রয়োজন হলে এর মাধ্যমে আরোপিত অর্থদণ্ড আদায়ে অভিযুক্তকে যৌক্তিক সময় ও সুযোগ প্রদান করতে হবে। এ ছাড়া মোবাইল কোর্ট আইনের ১৫ ধারা রহিত বা সংশোধন করে শুধু সংসদ কর্তৃক আইনের তপশিল সংশোধনের বিধান প্রণয়ন করা আবশ্যক।
এতে ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশের বিরুদ্ধে সরাসরি সংশ্লিষ্ট দায়রা জজ আদালতে আপিল দায়েরের বিধান করতে এবং আপিল দায়েরের অধিকার যাতে কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা যায়, তার জন্য দণ্ডাদেশ প্রদানের পর সর্বোচ্চ ২ (দুই) কর্মদিবসের মধ্যে অভিযুক্তকে আদেশের নকল সরবরাহ নিশ্চিতের বিধান করার কথা বলা হয়েছে।
সুপ্রিম কোর্টে বিচারক নিয়োগ ও শৃঙ্খলা:
প্রধান বিচারপতি নিয়োগের একক ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে রাখার সাংবিধানিক বিধান সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, ‘বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা সমুন্নত রাখা এবং কার্যকারিতা নিশ্চিত করা অনেকাংশে নির্ভর করে বিচার বিভাগের নেতৃত্বদানকারী তথা শীর্ষ ব্যক্তি হিসেবে প্রধান বিচারপতির ওপর। প্রধান বিচারপতির নিয়োগকে নির্বাহী কর্তৃপক্ষের প্রভাবমুক্ত করার লক্ষ্যে সংবিধানে এই মর্মে বিধান থাকা প্রয়োজন যে, রাষ্ট্রপতি আপিল বিভাগের কর্মে প্রবীণতম বিচারককেই প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করবেন। অর্থাৎ প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ বা অন্য কোনো বিকল্প পদ্ধতি রাখা যাবে না।’ আপিল বিভাগের বিচারপতি সাতজন নির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়েছে প্রতিবেদনে। এতে আরও বলা হয়েছে, ‘প্রধান বিচারপতির প্রয়োজনীয়তা অনুসারে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিচারক সময়ে সময়ে হাইকোর্ট বিভাগে নিয়োগ করা হবে।’ প্রধান বিচারপতি ব্যতীত অন্যান্য বিচারক নিয়োগের জন্য প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে ৯ সদস্যবিশিষ্ট ‘সুপ্রিম কোর্ট জাজেস অ্যাপয়েনমেন্ট কমিশন’ (সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ কমিশন) নামে একটি কমিশন গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগে এই নিয়োগ কমিশনের মতামতই প্রাধান্য পাবে। ৯ সদস্যবিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিশন হাইকোর্ট বিভাগে অতিরিক্ত বিচারক পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া পরিচালনা করবে।
‘স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস গঠন’:
সরকারি মামলা পরিচালনার জন্য রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস গঠন প্রস্তাব করা হয়েছে কমিশনের প্রতিবেদনে। এতে বলা হয়েছে, অ্যাটর্নি জেনারেলের পদকে একটি সাংবিধানিক পদ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে মূলত সরকারি স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিপুলসংখ্যক মামলা পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বিবেচনা করে। কিন্তু তাকে সহায়তা করার জন্য তিনটি স্তরে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আইন কর্মকর্তা নিয়োগ করা হলেও তাদের বিষয়ে সংবিধানে কোনো কিছু উল্লেখ করা হয়নি। এ ছাড়া জেলা পর্যায়ের আদালতগুলোয় সরকারি স্বার্থসংশ্লিষ্ট মামলা পরিচালনার জন্য তিনটি স্তরের পাবলিক প্রসিকিউটর এবং দুটি স্তরের গভর্নমেন্ট প্লিজার রয়েছেন। অ্যাটর্নি জেনারেলসহ সব স্তরের আইন কর্মকর্তা নিযুক্ত হয়েছেন মূলত রাজনৈতিক বিবেচনায় এবং অপ্রতুল আইনি কাঠামোর আওতায়। আইন কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পালন বিষয়ে জবাবদিহির কোনো আইনি কাঠামো নেই। যোগ্যতা বা দক্ষতা বা সততা নয়, মূলত আইন কর্মকর্তাদের নিয়োগকে বিবেচনা করা হয় রাজনৈতিক আনুগত্যের পুরস্কার হিসেবে। সামগ্রিকভাবে বিভিন্ন পর্যায়ের আইন কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পালনের মান মোটেও সন্তোষজনক নয়। বিচারব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থাহীনতা এবং জনস্বার্থ ক্ষুণ্ন হওয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে ওপরে বর্ণিত পরিস্থিতি। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য একটি স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন বলে কমিশন মনে করে।
স্বতন্ত্র তদন্ত সংস্থা গঠন:
কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় তদন্ত একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। ফৌজদারি মামলার গতি প্রকৃতি এবং ফল প্রাথমিকভাবে তদন্ত প্রতিবেদনের ওপর নির্ভরশীল। তদন্ত কর্মকর্তা সৎ, সাহসী, দক্ষ ও পেশাদার না হলে তদন্ত প্রতিবেদনে নানারকম দুর্বলতা থেকে যায়। তা ছাড়া তদন্ত প্রতিবেদনে অনেকক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব হচ্ছে, আবার অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হচ্ছে না। তদন্ত কার্যক্রমের এসব সমস্যার কারণে বেশিরভাগ ফৌজদারি মামলায় আসামি খালাস পাচ্ছে।
এতে বলা হয়েছে, তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্যও পুলিশের কোনো নিবেদিত একক ইউনিট নেই; বরং একাধিক বিভাগকে একই ধরনের কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এর ফলে পুলিশের বিদ্যমান তদন্ত ব্যবস্থা যথেষ্ট সুসংগঠিত ও সুদক্ষ নয়। মামলার তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনার সময় সরকারি প্রসিকিউটর কর্তৃক তদারকির সুনির্দিষ্ট কোনো ব্যবস্থা নেই। ফলে সমন্বয়ের অভাবে অনেক ক্ষেত্রেই যথাযথ সাক্ষ্যপ্রমাণ ছাড়াই আদালতে মামলার বিচার শুরু হয় এবং শেষ পর্যন্ত অপরাধীরা ছাড়া পেয়ে যায়। প্রচলিত তদন্ত ব্যবস্থা এবং তাতে নিয়োজিত জনবলকে সুসংগঠিত করার মাধ্যমে বিচার ব্যবস্থায় তদন্ত প্রক্রিয়ার যথাযথ ভূমিকা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি স্বতন্ত্র, কার্যকর, দক্ষ, নির্ভরযোগ্য, জনবান্ধব এবং প্রভাবমুক্ত তদন্ত সংস্থা গঠন প্রয়োজন বলে কমিশন মনে করে।
দুর্নীতি প্রতিরোধ ও স্বচ্ছতা-জবাবদিহি:
বিচার বিভাগকে দুর্নীতিমুক্ত রাখতে কয়েকটি পদক্ষেপ জরুরিভাবে নেওয়া প্রয়োজন বলে সুপারিশে উল্লেখ করা হয়েছে। কমিশন বলেছে, তিন বছর পরপর সুপ্রিম কোর্ট এবং অধস্তন আদালতের বিচারকদের সম্পত্তির বিবরণ সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে পাঠানো এবং তা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জনগণের সামনে প্রকাশ করতে হবে। জেলা পর্যায়ের আদালতের বিচারকদের স্বাধীনতা, নিরপেক্ষতা ও কার্যকর ভূমিকা নিশ্চিত করতে কয়েকটি প্রস্তাব তুলে ধরা হয়েছে প্রতিবেদনে। আইনগত সহায়তা কার্যক্রমের প্রসারের বিষয়ে বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন বলেছে, জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার বিদ্যমান সেবাগুলোর পরিধি বাড়িয়ে আইনি সহায়তার পাশাপাশি মীমাংসা ও মধ্যস্থতার মাধ্যমে মামলা ও বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্র সৃষ্টি করে মধ্যস্থতার কার্যক্রমকে দেশে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এজন্য এই সংস্থাকে একটি অধিদপ্তরে রূপান্তর করতে হবে। এ ছাড়া সংশ্লিষ্ট আইন রহিত করে একটি সময়োপযোগী আইন প্রণয়ন করা যেতে পারে।কালবেলা