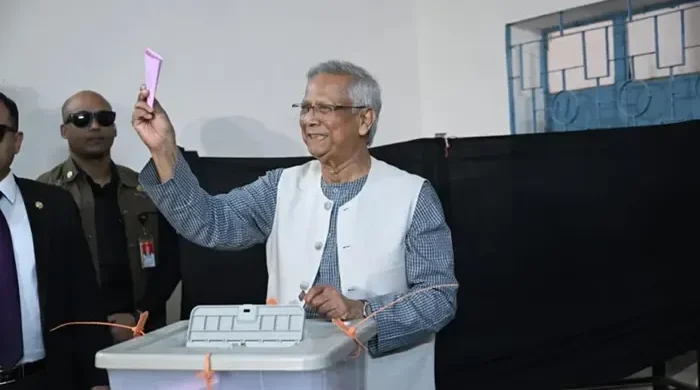পাহাড়ে হার্ডলাইনে সরকার

- আপডেট সময় সোমবার, ৮ এপ্রিল, ২০২৪
- ৩৪২ দেখা হয়েছে


ড. মাহফুজ পারভেজ:- শান্তিচুক্তির (১৯৯৭) পর সবচেয়ে বড় আকারের সশস্ত্র শোডাউনের প্রতিক্রিয়ায় পাহাড়ে হার্ডলাইনে সরকার। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও সেনাবাহিনীর প্রধানসহ বিভিন্ন সংস্থার শীর্ষ কর্মকর্তারা বান্দরবানের অকুস্থল পরিদর্শন করেছেন। তারপরই শুরু হয়েছে সর্বাত্মক অপারেশন। আটক হয়েছে কেএনএফ‘র প্রভাবশালী নেতাসহ অনেকেই।
১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি-পূর্ব জাতিগত হিংসা, রক্তপাত, হানাহানি ও সংঘাতময় পরিস্থিতি নিয়ে প্রফেসর ড. হুমায়ুন আজাদ সরজমিন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। নিজের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী গ্রন্থের একটি সুন্দর শিরোনাম দিয়েছিলেন তিনি: ‘পাবর্ত্য চট্টগ্রাম: সবুজ পাহাড়ের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হিংসার ঝরনাধারা’।
বইয়ের শুরুতে, ভূমিকার বদলে ‘অসুস্থ আহত সুন্দর’ শিরোনামের উপক্রমনিকাতে তিনি উল্লেখ করেন, বাংলাদেশের এক রূপময় খণ্ড, পার্বত্য চট্টগ্রাম, তিন দশক ধ’রে অসুস্থ আহত। কী হচ্ছে সেখানে বাঙালি তা ভাল ক’রে জানে না, তাদের জানারও আগ্রহ কম; এবং সরকারগুলোও, এক সময়, পালন করতো সন্দেহজনক নীরবতা। অস্পষ্টভাবে জানতাম আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়িরা চান স্বাধীনতা বা স্বায়ত্তশাসন; এবং তারা বিদ্রোহ করেছেন বাংলাদেশের বিরুদ্ধে। পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে অধিকাংশ বাঙালির মতো আমিও জানতাম সামান্যই; তবে এক দশক আগে তাদের পক্ষে লিখেছিলাম একটি আবেগকাতর রচনা; এবং অনেক অনামা পাহাড়ি পত্রলেখক আমাকে তাদের স্বপ্নের জুম্মল্যান্ডের নাগরিকত্বও দিয়েছিলেন।” সরেজমিনে ঘুরে এসে এবং দীর্ঘদিন ধরে পর্যবেক্ষণ করে হুমায়ুন আজাদ তাঁর আগের অবস্থান থেকে সরে আসেন। নতুন মত তিনি বিশ্লেষণ করেছেন পুরো বই জুড়ে। হুমায়ুন আজাদ স্পষ্টত বলেছেন, এসব দাবি পূরণ হবার নয়, জুম্মল্যান্ডের দাবি আসলে অবাস্তব।
অবাস্তব বলেই সংঘাত বিজয়ী হয়নি।
শান্তিচুক্তি সম্পন্ন হয়েছে পাহাড়ে। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি বা ‘পিসিজেএসএস‘ এবং তাদের সশস্ত্র গ্রুপ ‘শান্তিবাহিনী‘ প্রায় তিন যুগের রাজনৈতিক ও সামরিক পন্থায় লড়াই বন্ধ করে ১৯৯৭ সালে সরকারের সঙ্গে শান্তিচুক্তিতে উপনীত হয়। কিন্তু সংঘাত থেকে শান্তির পথে পার্বত্য চট্টগ্রামের অগ্রযাত্রা কণ্টকমুক্ত হয়নি। শান্তি বিরোধী নানা গোপন কার্যক্রম এখনো তৎপর। যারা হিংসা ও সন্ত্রাস বাড়াচ্ছে। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে ‘শান্তি চুক্তি’ ও ‘স্থায়ী শান্তি’ প্রসঙ্গ দুটি আবার গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং নতুন সশস্ত্র কর্মকাণ্ডের উত্থানে পরিস্থিতি আবার ক্রমেই জটিল আকার ধারণ করছে।
সরকারের সঙ্গে চুক্তি করার কিছুদিন পর পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি বা ‘পিসিজেএসএস‘ ভেঙে চুক্তি-বিরোধী গ্রুপ ইউপিডিএফ বের হয়ে যায়, যারা আবার অস্ত্র হাতে তুলে নেয়। পরে জনসংহতি ভেঙে দুই গ্রুপ এবং ইউপিডিএফ ভেঙে দুই গ্রুপ, তথা মোট চারটি গ্রুপ পার্বত্য চট্টগ্রামে রাজনৈতিক ও সশস্ত্র পন্থায় সরব থাকে। যাদের কেউ কেউ নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাসী। কেউ কেউ সশস্ত্র পন্থায়। তবে, তাদের সশস্ত্র পন্থা চাঁদাবাজি, অপহরণ, পাড়া-মহল্লায় লুটপাট কিংবা আধিপত্য বিস্তারের জন্য অন্য গ্রুপগুলোর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হলেও সরকার বা প্রশাসনকে বড় আকারের চ্যালেঞ্জ দেয়নি।
সরাসরি চ্যালেঞ্জ দিয়েছে পঞ্চম আরেকটি গ্রুপ, যাদের নাম কেএনএফ বা কুকি-চিন গোষ্ঠী। পার্বত্য চট্টগ্রামের ছোট-বড় ১৩টি উপজাতি বা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্যে যারা অধিকতর ক্ষুদ্রতর তাদের সমন্বয়ে এই গ্রুপ গঠিত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, জনসংহতি ও শান্তি বাহিনীর সশস্ত্র সংগঠনে পাহাড়ের প্রধান উপজাতি গোষ্ঠী চাকমা-মারমা-ত্রিপুরা ছাড়া বাকী অন্যান্য ক্ষুদ্রতর নৃগোষ্ঠীর তেমন কোনো অংশগ্রহণ ছিলো না। নেতৃত্ব পর্যায়ে তো নয়ই। ১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৮৩ সালের ১৪ জুন পর্যন্ত শান্তি বাহিনীর ১২ জনের যে নেতৃত্বের প্যানেল ছিলো, তার কোনো স্থানেই কুকি তথা বম, লুসাই, পাংখো, খুমি, খেয়াং, মুরং ইত্যাদি উপজাতি গোষ্ঠীর কোনোই প্রতিনিধিত্ব নেই। কেএনএফ উত্থানকালে পার্বত্য চট্টগ্রামে আভ্যন্তরীণ বৈষ্যমের বিরুদ্ধে কথা বলে। চাকমা-মারমা-ত্রিপুরা জাতিগোষ্ঠীর আগ্রাসন থেকে অন্যান্য ক্ষুদ্র উপজাতিদের ভাষা, সংস্কৃতি, রাজনৈতিক অধিকার রক্ষারও ডাক দেন।
তবে, আত্মপ্রকাশের কিছুদিন পরই কেএনএফ বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি, বরকল, জুরাছড়ি, বিলাইছড়ি এবং বান্দরবান জেলার রুমা, রোয়াংছড়ি, থানচি, লামা ও আলীকদম– এই ৯টি উপজেলা নিয়ে পৃথক স্বায়ত্তশাসিত রাজ্যের দাবি তোলে সামাজিক মাধ্যমে, যার নেতৃত্বে থাকেন নাথান বম, যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের ভাস্কর্য বিভাগের স্নাতক এবং জনসংহতির ছাত্র সংগঠনের সাবেক নেতা।
ঐতিহ্যগতভাবে বাংলাদেশের কুকি, ভারতের মিজো ও মিয়ানমারের চিন নিজেদের একই নৃগোষ্ঠী মনে করে। নৃবিজ্ঞানিরা এই তিন জাতিগোষ্ঠীকে একত্রে ‘জো’ অভিহিত করেন। এই ‘জো’ জাতীয়তাবাদও বর্তমানে বেশ আলোচিত। বাংলাদেশে কুকি সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শাখা বম, পাংখোয়া, লুসাই, খিয়াং, ম্রো ও খুমি নামে পরিচিত। কেএনএফ সংগঠনটি মূলত বম জনগোষ্ঠীনির্ভর (জনসংখ্যা প্রায় ১৩ হাজার) হলেও তারা পার্বত্য চট্টগ্রামের মূলত খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বী ৬টি জাতিগোষ্ঠীর (মোট জনসংখ্যা প্রায় ৪২ হাজার) প্রতিনিধিত্ব দাবি করে। যাহোক, নৃতাত্ত্বিক সংযোগের জন্যই ভারতের মণিপুর, মিজোরাম ও মিয়ানমারের চিন প্রদেশের ঘটনাপ্রবাহ পার্বত্য চট্টগ্রামকেও প্রভাবিত করতে পারে। কেএনএফের সশস্ত্র উত্থানের পেছনে ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনগুলোর অনুপ্রেরণা ও সহানুভূতি কতখানি, তা জানা জরুরি।
অতীতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি বা ‘পিসিজেএসএস‘ যখন সশস্ত্র শাখা ‘শান্তিবাহিনী‘ গঠন করে, তখন কেউই মনে করেনি যে, সরকারি নীতি প্রতিরোধ করার জন্য পাহাড়ে বিদ্রোহীরা সংগঠিত হচ্ছে। ১৯৭৬-৭৭ সালে যখন তারা বাজার, পুলিশ ফাঁড়ি ইত্যাদিতে হামলা চালায়, তখনও অনেকে মনে করেছেন, বিষয়টি আইন-শৃঙ্খলার সমস্যা। শান্তিবাহিনীর বিদ্রোহীরা প্রতিবেশী ভারতের ত্রিপুরায় লুকিয়ে ছিল, যেখানে তারা নিজেদেরকে প্রশিক্ষণ ও সজ্জিত করেছিল।
সাবেক শান্তিবাহিনীর অভিযানগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, উওর-পূর্বে মিজোরাম বরাবর বা নদীপথে যাতায়াত করতে হয় এমন স্থানগুলোতো তাদের প্রভাব বেশি ছিল এবং সেখানে হতাহতের সংখ্যা বা আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যাও ছিল বেশি। যেমন: এস ব্যান্ড, বরকল, ফারুয়া, ঘণ্টিছড়া, কুকিছড়া ইত্যাদি এলাকা। শান্তি বাহিনীর সীমান্ত পেরিয়ে বেশির ভাগ ক্যাম্প (হেড কোয়ার্টারসহ) ছিলো ত্রিপুরা রাজ্যে; যেখানে একটি বিরাট সংখ্যক চাকমা ও ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী বাস করে। ভারতের এই রাজ্য থেকেই তারা যাবতীয় সাহায্য সহযোগিতা পেয়ে ছিল। শান্তিবাহিনীর মূল স্থায়ী ক্যাম্পগুলো এই ত্রিপুরা রাজ্যেই অবস্থিত ছিল।
সাম্প্রতিক নাশকতার বিষয়ে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ, ২রা এপ্রিল মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর রুমা উপজেলায় সোনালী ব্যাংকে হানা দেয় কেএনএফ। এ সময় তারা পুলিশ ও আনসার বাহিনীর ১৪টি অস্ত্র এবং ব্যাংকের শাখা ব্যবস্থাপক নেজামউদ্দিনকে তুলে নিয়ে যায়। ১৬ ঘণ্টা না যেতেই ৩ এপ্রিল দুপুরে একই সশস্ত্র গোষ্ঠী থানচি উপজেলার কৃষি ও সোনালী ব্যাংক থেকে প্রায় ১৭ লাখ টাকা লুট করে। পরদিন ৪ এপ্রিল রাত সাড়ে ৮টার দিকে থানচি থানা লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে কেএনএফ। এই তিন হামলার ঘটনা অনেক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। প্রথমত, কেএনএফের সঙ্গে বান্দরবানের শান্তি প্রতিষ্ঠা কমিটির দফায় দফায় আলোচনা চলছিল। এমন পরিস্থিতিতে তারা কেন শহরের ভেতরে সরকারি স্থাপনায় এ ধরনের আক্রমণ পরিচালনা করল? দ্বিতীয়ত, রুমা ও থানচিতে কি নিরাপত্তা শৈথিল্য ও গোয়েন্দা ব্যর্থতা ছিল? তৃতীয়ত, সীমান্তের বাইরে তাদের কোনো বেস বা শক্ত আস্তানা আছে কিনা? চতুর্থত, মিয়ানমারে চলমান সশস্ত্র সংঘাতের মাধ্যমে তারা শক্তি সঞ্চয় করছে কিনা? এবং বাংলাদেশের বান্দরবানের সীমানার পাশে ভারতের মনিপুর, মিজোরামে স্বগোত্রীয়দের সঙ্গে কেএনএফ‘র নেতাদের যোগাযোগ আছে কিনা? পাহাড়ে সশস্ত্র নাশকতা নির্মূল করতে হলে সংশ্লিষ্ট সকল প্রশ্ন, আশঙ্কা ও সম্ভাবনাকেও খতিয়ে দেখা আবশ্যক।
পার্বত্য চট্টগ্রামে এখন একাধিক আঞ্চলিক সংগঠন সক্রিয় রয়েছে। চাঁদাবাজি ও আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে এসব সংগঠনের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাতে প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। আবার কোনো কোনো আঞ্চলিক সংগঠন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। ফলে শান্তিচুক্তির আওতায় শান্ত পাহাড়ে ফের অশান্তির ভীতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব ঘটনার ফলে প্রাণ বাঁচাতে এলাকা ছেড়েছে বহু উপজাতি পরিবার। পার্শ্ববর্তী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আশ্রয় নেওয়া পরিবারগুলোকে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে খাদ্য সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। উল্লেখ্য, ২০২২ সালে শুধু বান্দরবানে গোষ্ঠীগুলোর দ্বন্দ্ব-সংঘাতে খুন হয়েছিল ১৪ জন। পরের বছরগুলোতে হতাহলের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়েছে। এমন সংঘাত অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে আরো প্রাণহানির আশঙ্কা করা হচ্ছে।
ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের মতো নিরাপত্তার ঝুঁকিপূর্ণ এবং কৌশলগত এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজটি একটি চলমান প্রক্রিয়া, যা প্রতিনিয়ত চর্চা ও কার্যক্রমের মাধ্যমে এগিয়ে নেয়া জরুরি। সরকারের বিভিন্ন সংস্থা, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিকে এ লক্ষ্যে অব্যাহতভাবে কাজ করতে হবে। ‘শান্তির পক্ষে’ ও ‘শান্তির জন্য’ সহায়ক পরিবেশ ও পরিকাঠামো গঠন এবং নাগরিক সমাজে আস্থা, বিশ্বাস, সৌহার্দ্য, নিরাপত্তা ও পারস্পরিক সমঝোতা বজায়ের মাধ্যমে মজবুত করতে হয় শান্তির গতিবেগ।
‘চুক্তি’ স্থায়ী শান্তির পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এর গুরুত্ব অপরিসীম। পাশাপাশি সময়ের পরিবর্তনে ক্রমে ক্রমে তৈরি হওয়া শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিতকারী গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলোর প্রতিও নজর দেওয়া অপরিহার্য। এজন্য সরকারের সঙ্গে পাহাড়ের বাঙালি ও উপজাতি গোষ্ঠীগুলোকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। সরকারের বিভিন্ন সামরিক-বেসামরিক সংস্থাকে শান্তি, নিরাপত্তা ও জনস্বার্থ হানিকর প্রকাশ্য ও গোপন তৎপরতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সতর্ক, সজাগ থেকে নিরাপত্তা ও শান্তির পক্ষে উদ্যোগী ভূমিকা নিতে হবে। পাহাড়ের রাজনীতিবিদদেরকেও নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির পক্ষে শক্তিশালী অবস্থান নিয়ে সশস্ত্র কার্যক্রমের বিরুদ্ধে সরব হতে হবে।
বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ অংশ পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী শান্তি সকলেরই প্রত্যাশা। অশান্তির আগুন সকলের জন্যই বিপজ্জনক এবং অশান্তির কুফল ভয়াবহ ও ক্ষতিকর। অতীতে অশান্তির মারাত্মক পরিণাম দেখা গেছে। ফলে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সার্বক্ষণিক ভাবে একযোগে কাজ করার কোনো বিকল্প নেই। সন্ত্রাস বা অশান্তি নয়, আলাপ-আলোচনা, নিয়মতান্ত্রিকতা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ভিত্তিতে স্থায়ী শান্তির পথে অগ্রসর হওয়াই বিভ্রান্ত ও বিপথগামী পক্ষগুলোর জন্য কল্যাণকর। বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় সন্ত্রাসী রাজনীতির পরিসর নেই বললেই চলে। ফলে শান্তিপূর্ণ পন্থায় অগ্রসর হয়ে দাবি আদায়ে সচেষ্ট হওয়াই অধিকর লাভজনক।
লেখক: প্রফেসর, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও নির্বাহী পরিচালক, চট্টগ্রাম সেন্টার ফর রিজিওনাল স্টাডিজ, বাংলাদেশ (সিসিআরএসবিডি)।